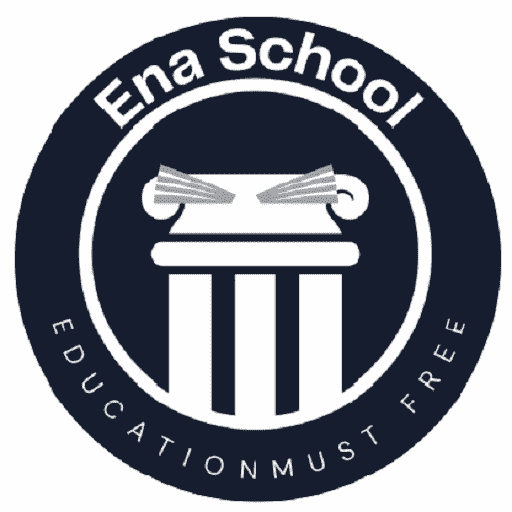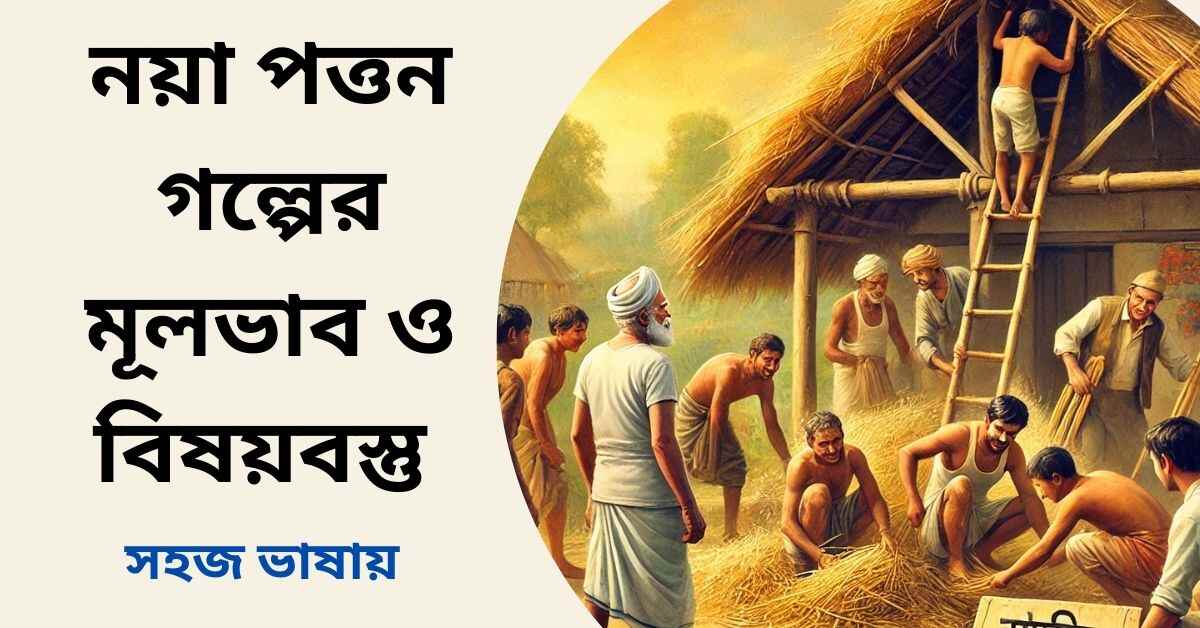জহির রায়হানের “নয়া পত্তন” গল্পটি গ্রামীণ সমাজের শিক্ষার সংকট, শোষণব্যবস্থা এবং সাধারণ মানুষের স্বাবলম্বী হওয়ার সংগ্রামকে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নিচে নয়া পত্তন গল্পের মূলভাব ও বিষয়বস্তু দেওয়া হল।
নয়া পত্তন গল্পের মূলভাব
জহির রায়হানের “নয়া পত্তন” গল্পটি গ্রামীণ সমাজের শিক্ষা সংকট ও সাধারণ মানুষের সংগ্রামের কাহিনী। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র শনু পণ্ডিত, একজন নিঃস্বার্থ শিক্ষক, যিনি তার ভাঙাচোরা স্কুলটি পুনরুদ্ধারের জন্য শহরে গিয়ে সরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় জমিদার চৌধুরীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু উভয় পক্ষই তাকে অপমানসহ প্রত্যাখ্যান করে। হতাশ হয়ে গ্রামে ফিরে এসে তিনি দেখেন, সাধারণ কৃষক-মজুররা নিজেদের উদ্যোগে স্কুলটি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে – কেউ দেয় ছন, কেউ বাঁশ, আবার কেউ শ্রম দিয়ে সহায়তা করে। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শুধু স্কুলের ভবনই গড়ে ওঠে না, বরং তারা চৌধুরীর নামফলক সরিয়ে সেখানে “শনু পণ্ডিতের ইস্কুল” লেখে, যা হয়ে ওঠে তাদের আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনচেতার প্রতীক। গল্পটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে যে, শাসক শ্রেণীর উপর নির্ভর না করে সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তিই পারে সামাজিক পরিবর্তন আনতে।
নয়া পত্তন গল্পের বিষয়বস্তু
শনু পণ্ডিত ভোরের ট্রেনে গ্রামে ফিরে আসেন এক করুণ চিত্র নিয়ে। তাঁর দেহ ন্যুজ, চুল রুক্ষ, মুখে বার্ধক্যের গভীর রেখা। শহরে গিয়ে তিনি সরকার ও জমিদার চৌধুরীর দ্বারস্থ হয়েছিলেন স্কুল পুনর্নির্মাণের জন্য সাহায্য চাইতে। কিন্তু শিক্ষা অফিসের বড় কর্তা শমসের খান তাঁকে অপমান করে বলেন, “হোটেল আর ইংলিশ স্কুল বানাতেই আমাদের টাকা ফুরিয়েছে।” চৌধুরীও টাকা দিতে অস্বীকার করেন। এই প্রত্যাখ্যান শনু পণ্ডিতকে গভীরভাবে আহত করে।
পথে ভাঙা স্কুলটি দেখে শনু পণ্ডিতের মনে পড়ে যায় পঁচিশ বছর আগের কথা। তরুণ বয়সে তিনি চৌধুরীর দেওয়া অনাবাদি জমিতে নিজের জমি বিক্রি করে এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন গ্রামের কেউই লেখাপড়া জানত না। স্কুলের নাম রাখা হয়েছিল “জুলু চৌধুরীর স্কুল” – নামফলকে চৌধুরীর নাম জ্বলজ্বল করত, যদিও আসল শ্রম ও ত্যাগ ছিল শনু পণ্ডিতের।
গ্রামবাসীরা শনু পণ্ডিতের ফিরে আসার খবরে জড়ো হয়। কেউ কেউ বলে, “লেখাপড়ার কী দরকার? আমাদের বাপ-দাদাও তো অশিক্ষিতই ছিল।” কিন্তু বুড়ো হাশমত, তোরাব আলী, তকু শেখের মতো মানুষরা জোর দিয়ে বলে, “আমরাই স্কুল গড়ে তুলব! কারো কাছে ভিক্ষা চাইব না!” তাদের চোখে জ্বলে নতুন স্বপ্ন।
গ্রামের প্রতিটি মানুষ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। কেউ দেয় ত্রিশ আঁটি ছন, কেউ সাত কুড়ি বাঁশ, কেউ শ্রম। তারা হাসতে হাসতে বলে, “এটা চৌধুরীর লাশ টানছি!” – শোষকের প্রতি তাদের বিদ্রূপ ফুটে ওঠে এই কথায়। শনু পণ্ডিতও বয়সের ভারে ন্যুজ হয়েও হাতে দা নিয়ে কাজে যোগ দেন।
স্কুল তৈরি শেষে তোরাব আলী চৌধুরীর নামফলক খুলে ফেলে। কাঠকয়লা দিয়ে লেখে “শনু পণ্ডিতের ইস্কুল”। এই দৃশ্য দেখে শনু পণ্ডিত প্রথমে লজ্জা পান, কিন্তু গ্রামবাসীরা জোর দিয়ে বলে এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। এটি শুধু নাম পরিবর্তন নয়, বরং সাধারণ মানুষের স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার প্রকাশ।
আরও পড়ুনঃ কাকতাড়ুয়া গল্পের মূলভাব ও বিষয়বস্তু – সত্যজিৎ রায়