মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য-এর এই অংশে মেঘনাদ (ইন্দ্রজিৎ) ও বিভীষণ-এর মধ্যকার তিক্ত সংলাপ রামায়ণের প্রচলিত নৈতিকতার বিপরীতে একটি ট্র্যাজিক ভাব প্রকাশ করে। নিচে বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ কবিতার মূলভাব ও ব্যাখ্যা দেওয়া হল।
বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ কবিতার মূলভাব
“বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ” কবিতাটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ থেকে নেওয়া হয়েছে, যেখানে মেঘনাদ তার চাচা বিভীষণকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেন। যুদ্ধের সময় মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে পূজা করছিলেন, তখন বিভীষণের সাহায্যে লক্ষ্মণ সেখানে প্রবেশ করে। মেঘনাদ বুঝতে পারেন, বিভীষণই রামের পক্ষ নিয়ে শত্রুদের লঙ্কায় ঢুকতে সাহায্য করেছেন। ক্ষুব্ধ মেঘনাদ বিভীষণকে বলেন, “তুমি আমাদের পরিবারেরই লোক হয়ে শত্রুদের পথ দেখালে?” তিনি বিভীষণকে স্মরণ করিয়ে দেন তাদের মহান বংশের কথা – রাবণ, কুম্ভকর্ণ এবং নিজের বীরত্বের কথা। মেঘনাদ প্রশ্ন করেন, “সিংহ কি কখনো শিয়ালের সাথে বন্ধুত্ব করে?” বিভীষণ উত্তর দেন, তিনি ধর্মের পক্ষ নিয়েছেন, কারণ রাবণের পাপেই লঙ্কার ধ্বংস আসছে। কিন্তু মেঘনাদ বলেন, “গুণহীন স্বজনও গুণবান শত্রুর চেয়ে ভালো।” মধুসূদন এখানে মেঘনাদকে বীর ও ট্র্যাজিক নায়ক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, আর রাম-লক্ষ্মণকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছেন। এই কবিতা দিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন, ধর্ম বা নীতির নামে স্বদেশ ও পরিবারের বিরুদ্ধে যাওয়াই সবচেয়ে বড় পাপ।
বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ কবিতার ব্যাখ্যা
| কবিতার লাইন | লাইনের ব্যাখ্যা |
| “এতক্ষণে”- অরিন্দম কহিলা বিষাদে- “জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল রক্ষঃপুরে।” | মেঘনাদ (যিনি ‘অরিন্দম’ বা শত্রুদমনকারী নামে পরিচিত) গভীর দুঃখের সুরে বলতে শুরু করেন। এই মুহূর্তে তিনি উপলব্ধি করছেন কীভাবে লক্ষ্মণ তাদের দুর্গে প্রবেশ করতে পেরেছে। তার কণ্ঠে বেদনার ছাপ স্পষ্ট, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছেন এই প্রবেশ সম্ভব হয়েছে বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে। |
| “হায়, তাত, উচিত কি তব এ কাজ,” | তিনি বিভীষণকে ‘তাত’ (চাচা/পিতৃব্য) সম্বোধন করে বলছেন, “হায়, চাচা, তোমার এই কাজ কি উচিত হয়েছে?” মেঘনাদ যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না যে তারই পরিবারের সদস্য এমন কাজ করেছেন। |
| “নিকষা সতী তোমার জননী,” | মেঘনাদ বিভীষণকে তার মা নিকষার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যিনি ছিলেন পবিত্র চরিত্রের অধিকারী। এই উক্তি দিয়ে তিনি বোঝাতে চাইছেন যে এমন সতী মায়ের সন্তান হয়ে বিভীষণ কীভাবে এই কাজ করতে পারলেন। |
| “সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? শূলীশম্ভুনিভ কুম্ভকর্ণ?” | তিনি প্রশ্ন করছেন, “তোমার ভাই রাবণ (রাক্ষসকুলের শ্রেষ্ঠ) এবং মহাদেবের মতো পরাক্রমশালী কুম্ভকর্ণের কথা কি ভুলে গেলে?” এখানে পূর্বপুরুষদের বীরত্ব ও সম্মানের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মেঘনাদ বোঝাতে চাইছেন যে তাদের বংশ এমন গৌরবময় যে এর মর্যাদা রক্ষা করা উচিত ছিল। |
| “ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী।” | মেঘনাদ নিজেকে ‘ইন্দ্রবিজয়ী’ হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন, তার বীরত্বের প্রমাণ দিচ্ছেন। তিনি বলতে চাইছেন, “আমি তোমারই ভাইপো, যে দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করেছে।” |
| “নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?” | তিনি ক্রোধভরে প্রশ্ন করছেন, “চাচা, নিজের ঘরের গোপন পথ তুমি চোর-ডাকাতদের দেখিয়ে দিলে?” এখানে ‘তস্কর’ বলতে রাম-লক্ষ্মণকে বোঝানো হয়েছে। |
| “চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?” | তিনি তীব্র অভিযোগ করছেন, “চণ্ডালদের (অপদার্থদের) তুমি রাজপ্রাসাদে এনে বসালে?” এখানে রাম-লক্ষ্মণকে চণ্ডাল বলা হয়েছে গভীর অবজ্ঞা প্রকাশের জন্য। মেঘনাদ বোঝাতে চাইছেন যে বিভীষণ অযোগ্য ব্যক্তিদের সম্মান দিয়েছেন। |
| “কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি পিতৃতুল্য।” | মেঘনাদ বলছেন, “তবে আমি তোমাকে গালি দিচ্ছি না, কারণ তুমি আমার গুরুজন, পিতার সমান।” |
| “ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,” | তিনি বিভীষণকে বলছেন, “পথ ছেড়ে দাও, আমি অস্ত্রাগারে যাব।” মেঘনাদ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে চান। |
| “পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,” “লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।” | তিনি তার সংকল্প প্রকাশ করছেন, “লক্ষ্মণকে (রামের ছোট ভাইকে) যমালয়ে পাঠাব।” মেঘনাদ বলছেন, “আজ যুদ্ধে লঙ্কার কলঙ্ক মোচন করব।” তিনি লঙ্কার সম্মান রক্ষার শপথ নিচ্ছেন। |
| “উত্তরিলা বিভীষণ, ‘বৃথা এ সাধনা'” | বিভীষণ মেঘনাদের যুদ্ধের প্রস্তুতিকে “নিষ্ফল প্রচেষ্টা” বলে উড়িয়ে দেন। তাঁর মতে, রামের বিরুদ্ধে লড়াই করা অর্থহীন। |
| “ধীমান। রাঘবদাস আমি” | বিভীষণ মেঘনাদকে “বুদ্ধিমান” (ধীমান) সম্বোধন করে স্বীকার করেন, “আমি রামের দাস”। এখানে তিনি নিজের আনুগত্যের স্পষ্ট ঘোষণা দেন এবং রামকে “রাঘব” (রঘুবংশীয়) বলে সম্মান দেখান। |
| “কী প্রকারে তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে অনুরোধ?” | তিনি যুক্তি দেন, “কীভাবে আমি রামের বিপক্ষে গিয়ে তোমার অনুরোধ রক্ষা করব?” |
| “উত্তরিলা কাতরে রাবণি” “‘হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!'” | রাবণের পুত্র (মেঘনাদ) বেদনাভরা কণ্ঠে জবাব দেন। মেঘনাদ বলেন, “হে চাচা, তোমার কথা শুনে আমি মরতে ইচ্ছুক!” |
| “‘রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে আনিলে এ কথা'” “‘তাত, কহ তা দাসেরে'” | মেঘনাদ ক্ষুব্ধ হয়ে প্রশ্ন করেন, “তুমি রামের দাস? এ কথা কীভাবে তোমার মুখে এল?” ব্যঙ্গাত্মকভাবে মেঘনাদ বলেন, “চাচা, এ দাসকে (আমাকে) বলো।” “দাসেরে” বলতে মেঘনাদ নিজেকে বোঝান। |
| “‘স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে'” | মেঘনাদ এক চমৎকার রূপক ব্যবহার করেন: “বিধাতা চাঁদকে স্থির আকাশে স্থাপন করেছেন।” তিনি ইঙ্গিত দেন যে, চাঁদ যেমন আকাশে স্থির, তেমনি রাক্ষসকুলের মর্যাদাও অবিচল থাকার কথা—কিন্তু বিভীষণ তা ভেঙে দিয়েছেন। |
| “‘পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি ধূলায়?'” | মেঘনাদ প্রশ্ন করেন, “চাঁদ কি কখনো ধুলায় গড়াগড়ি খায়?” অর্থাৎ, “আমাদের মতো মহান বংশের লোকেরা কি এভাবে অপমানিত হবে?” |
| “‘হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে'” | মেঘনাদ বিভীষণকে “রাক্ষসকুলের রথী” (যোদ্ধা) বলে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি কীভাবে ভুলে গেলে?”—অর্থাৎ, তোমার নিজের বংশের গৌরব ও কর্তব্যভুলে গেলে কীভাবে? |
| “কে তুমি? জনম তব কোন মহাকুলে?” | মেঘনাদ বিভীষণকে তীব্রভাবে জিজ্ঞাসা করছেন, “তুমি কে? কোন মহান বংশে তোমার জন্ম?” এই প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি বিভীষণের বংশগত মর্যাদা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যেন বলতে চান—এত মহান বংশে জন্মেও তুমি কীভাবে এই কাজ করলে? |
| “কে বা সে অধম রাম?” | তিনি রামকে “অধম” (নিকৃষ্ট) বলে আখ্যায়িত করে প্রশ্ন করেন, “সেই নীচ রাম কে?” এখানে মেঘনাদের অহংকার ও রামের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে। |
| “স্বচ্ছ সরোবরে করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে;” | মেঘনাদ একটি রূপক ব্যবহার করেন: “রাজহংস (মরাল) যেমন পরিষ্কার জলেই খেলা করে, পদ্মবনে বিচরণ করে।” তিনি বোঝাতে চান, উচ্চবংশীয়রা (তাদের মতো) কখনো নীচের সাথে মেলামেশা করে না। |
| “যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে, শৈবালদলের ধাম?” | তিনি জিজ্ঞাসা করেন, “সে (রাজহংস) কি কখনো পঙ্কিল জলে যায়, শেওলায় ভরা ডোবায়?” অর্থাৎ, “আমরা (রাক্ষসবংশ) কি কখনো রামের মতো নীচের সাথে যুক্ত হব?” |
| “মৃগেন্দ্র কেশরী, কবে, হে বীরকেশরী, সম্ভাষে শৃগালে মিত্রভাবে?” | আরেকটি রূপক: “সিংহ (মৃগেন্দ্র) কি কখনো শৃগালের (শিয়াল) সাথে বন্ধুত্ব করে?” মেঘনাদ বিভীষণকে “বীরকেশরী” (যোদ্ধাসিংহ) সম্বোধন করে বলছেন, “তুমি সিংহ, রাম শৃগাল—তোমাদের মিত্রতা কীভাবে সম্ভব?” |
| “অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি, অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।” | ব্যঙ্গাত্মকভাবে মেঘনাদ বলেন, “আমি অজ্ঞ (মূর্খ), তুমি মহাজ্ঞানী—তোমার অজানা কিছু নেই।” এখানে তিনি বিভীষণের বিচারবুদ্ধিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছেন, যেন বলতে চান—এত জ্ঞানী হয়েও তুমি ভুল সিদ্ধান্ত নিলে! |
| “ক্ষুদ্রমতি নর, শুর, লক্ষ্মণ; নহিলে অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?” | তিনি লক্ষ্মণকে “ক্ষুদ্রমতি” (সংকীর্ণচেতা) ও “অস্ত্রহীন যোদ্ধা” বলে আক্রমণ করেন, প্রশ্ন রাখেন—”লক্ষ্মণ কি সাধারণ যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করে? না, সে শুধু নিরস্ত্রদের (আমার মতো) উপরই আক্রমণ করে!” |
| “কহ, মহারথী, এ কি মহারথী-প্রথা?” | মেঘনাদ বিভীষণকে “মহারথী” (মহাযোদ্ধা) সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করেন, “এটা কি মহাযোদ্ধাদের আচরণ? (নিরস্ত্রের উপর আক্রমণ?)” |
| “নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে এ কথা!” | তিনি বিদ্রূপ করে বলেন, “লঙ্কায় শিশু নেই যে এ কথা শুনে হাসবে!” অর্থাৎ, “এই যুক্তি এতই হাস্যকর যে শুধু শিশুরাই এতে হাসতে পারে!” |
| “ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া এখনি!” “দেখিব আজি, কোন্ দেববলে, বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি!” | মেঘনাদ বিভীষণকে পথ ছাড়তে বলেন, “আমি এখনই ফিরে আসব!” তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন, “আজ দেখব, কোন দেবশক্তিতে লক্ষ্মণ (সৌমিত্রি) আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করে!” মেঘনাদের আত্মবিশ্বাস এখানে প্রজ্বলিত—তিনি বিশ্বাস করেন, ন্যায্য যুদ্ধে তাকে হারানো অসম্ভব। |
| “বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি!” | মেঘনাদ বিদ্রূপ করে বলেন, “লক্ষ্মণ (সৌমিত্রি) কি সত্যিই আমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারবে?” এখানে “কুমতি” শব্দে লক্ষ্মণের বুদ্ধিকে তুচ্ছ করা হয়েছে। মেঘনাদের আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠেছে – তিনি বিশ্বাস করেন, ন্যায্য যুদ্ধে লক্ষ্মণ তার সামনে টিকতে পারবে না। |
| “দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ, রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের!” | মেঘনাদ বিভীষণকে স্মরণ করিয়ে দেন: “দেবতা, দৈত্য ও মানুষের যুদ্ধে তুমি নিজ চোখে দেখেছ এই ‘দাসের’ (আমার) পরাক্রম!” “দাস” শব্দ ব্যবহার করে মেঘনাদ বোঝান, যদিও তিনি নিজেকে বিভীষণের সামনে বিনয়ী করছেন,কিন্তু আসলে তিনি একজন অপরাজেয় যোদ্ধা। |
| “কী দেখি ডরিবে এ দাস হেন দুর্বল মানবে?” | তিনি প্রশ্ন করেন, “কী দেখে এই দাস (আমি) এমন দুর্বল মানুষকে (লক্ষ্মণকে) ভয় পাবে?” |
| “নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগলভে পশিল দন্তী;” | মেঘনাদ অভিযোগ করেন, “লক্ষ্মণ (দন্তী/দাম্ভিক) ঔদ্ধত্য দেখিয়ে আমাদের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ঢুকেছে।” |
| “আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।” | তিনি বিভীষণকে বলেন, “আমাকে আদেশ দাও, আমি এই নীচ মানুষটিকে (লক্ষ্মণকে) শাস্তি দেব।” |
| “তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে বনবাসী!” | মেঘনাদের ক্ষোভ ফেটে পড়ে: “হে চাচা, তোমার জন্মভূমিতে সেই বনবাসী (রাম) পদার্পণ করছে!” |
| “হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে ভ্রমে দুরাচার দৈত্য?” | তিনি বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করেন, “হে ভাগ্যনির্মাতা, স্বর্গের বাগানে কি দুষ্ট দৈত্য ঘুরে বেড়ায়?” অর্থাৎ, “আমাদের পবিত্র লঙ্কায় কি রামের মতো অধর্মীর স্থান আছে?” |
| “প্রফুল্ল কমলে কীটবাস?” | রূপক: “ফুটন্ত পদ্মে কি কীট বাস করতে পারে?” অর্থাৎ মেঘনাদ বোঝাতে চান, রামের মতো নীচ ব্যক্তি লঙ্কার মতো মহান স্থানে থাকার অযোগ্য। |
| “কহ তাত, সহিব কেমনে হেন অপমান আমি, ভ্রাতৃ-পুত্র তব?” | মেঘনাদ বিভীষণকে আবেগাপ্লুতভাবে জিজ্ঞাসা করেন, “বলো চাচা, আমি কীভাবে এই অপমান সহ্য করব? আমি তোমার ভাইয়ের ছেলে!” |
| “তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?” | শেষে তিনি বিভীষণকে সরাসরি প্রশ্ন করেন, “হে রাক্ষসকুলের রত্ন (রক্ষোমণি), তুমিও কীভাবে এই অপমান সহ্য করছ?” |
| “মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী” | রূপক: “যেমন মন্ত্রবলে সাপ মাথা নত করে”, তেমনি বিভীষণও লজ্জায় ও অনুতাপে মাথা হেঁট করেছেন। |
| “মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী” | বিভীষণের মুখ লজ্জায় মলিন হয়েছে। “রথী” (যোদ্ধা) শব্দটি ব্যবহার করে বোঝানো হয়েছে যে, যদিও তিনি একজন বীর, কিন্তু এখন তিনি নৈতিক পরাজয়বোধে আক্রান্ত। |
| “রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে” | এখানে চরিত্রদের সম্পর্ক স্পষ্ট করা হয়েছে: বিভীষণ রাবণের ছোট ভাই, আর মেঘনাদ রাবণের পুত্র (মেঘনাদের) দিকে তাকিয়ে আছেন। |
| “‘নহি দোষী আমি, বৎস। বৃথা ভর্ৎস মোরে'” | বিভীষণ স্নেহের সাথে মেঘনাদকে “বৎস” (পুত্র) সম্বোধন করে বলছেন, “আমি নির্দোষ। আমাকে বৃথা তিরস্কার করো না।” |
| “‘নিজ কর্ম-দোষে, হায়, মজাইলা এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি!'” | বিভীষণ মর্মান্তিক সত্য উচ্চারণ করেন: “রাবণ নিজের কুকর্মের ফলেই সোনার লঙ্কা ও নিজেকে ধ্বংস করেছেন।” “কনক-লঙ্কা” শব্দটি লঙ্কার সমৃদ্ধি ও বিলাসিতার প্রতীক, যা এখন ধ্বংসের মুখে। |
| “‘বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী'” | দেবতারা পাপ থেকে দূরে থাকে। কিন্তু এখন লঙ্কা পাপে পূর্ণ। |
| “‘প্রলয়ে যেমতি বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে!'” | রূপক: “যেমন প্রলয়কালে পৃথিবী জলে ডুবে, তেমনি লঙ্কা পাপের কালো জলে ডুবে যাচ্ছে।” |
| “‘রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী তেই আমি'” | বিভীষণ তার অবস্থান স্পষ্ট করেন: “আমি রামের শরণ নিয়েছি নিজেকে রক্ষা করার জন্য।” |
| “‘পরদোষে কে চাহে মজিতে?'” | তিনি যুক্তি দেন: “অন্যরের দোষে কে ডুবে মরতে চায়?” |
| “রুষিলা বাসবত্রাস” | মেঘনাদ (যিনি ইন্দ্রকেও ভয় দেখিয়েছেন, তাই “বাসবত্রাস”) ক্রোধে ফেটে পড়লেন। |
| “গম্ভীরে যেমতি নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমুতেন্দ্র কোপি” | এখানে মেঘনাদের কণ্ঠস্বরকে গভীর রাতের মেঘের গর্জনের সাথে তুলনা করা হয়েছে: “জীমুতেন্দ্র” = মেঘরাজ “কোপি” = ক্রোধী |
| “কহিলা বীরেন্দ্র বলী” | মেঘনাদকে “বীরদের রাজা” বলা হয়েছে, যা তার যোদ্ধাসুলভ গুণাবলীকে নির্দেশ করে। |
| “‘ধর্মপথগামী'” | মেঘনাদ বিভীষণকে বিদ্রূপ করে “ধর্মের পথচারী” বলেন। কারণ মেঘনাদের মতে, বিভীষণের এই ধর্মানুসরণ আসলে বিশ্বাসঘাতকতা। |
| “হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে তুমি;” | মেঘনাদ বিদ্রূপের সুরে বিভীষণকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন—”হে রাক্ষসরাজের ভাই, তুমি তো বিশ্ববিখ্যাত!” বিভীষণ এখন রামভক্ত হিসেবে পরিচিত, যা মেঘনাদের মতে বংশের জন্য কলঙ্ক। |
| “কোন্ ধর্ম মতে, কহ দাসে, শুনি, জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি, এ সকলে দিলা জলাঞ্জলি?” | তিনি সরাসরি প্রশ্ন করেন: “কোন ধর্মে ভ্রাতৃত্ব, জাতি-জ্ঞাতির বন্ধন ত্যাগ করা যায়? বলো তো!” মেঘনাদের যুক্তি—ধর্ম যাই হোক, রক্তের বন্ধন ও স্বদেশপ্রেম তার ঊর্ধ্বে। |
| “শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!” | মেঘনাদ শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন: “গুণবান শত্রু থাকলেও গুণহীন আত্মীয়ই শ্রেয়; পর সর্বদা পর (শত্রু সর্বদা শত্রু)!” |
| “এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে?” | তিনি বিভীষণকে “রক্ষোবর” (রাক্ষসশ্রেষ্ঠ) সম্বোধন করে বিদ্রূপ করেন: “এ শিক্ষা (বিশ্বাসঘাতকতা) তুমি কোথায় পেলে?” |
| “কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে, হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে?” | মেঘনাদ হতাশাভরে বলেন: “তোমাকে গালি দেওয়া বৃথা! তুমি যাদের সাথে থাকো (রামের দল), তাদের কাছ থেকে বর্বরতা ছাড়া আর কী শিখবে?” |
| “গতি যার নীচসহ, নীচ সে দুর্মতি।” | তিনি একটি প্রবাদবাক্য ব্যবহার করেন: “যে নীচের সাথে চলবে, তার বুদ্ধিও নীচ হবে।” এটি রাম-লক্ষ্মণকে “নীচ” এবং বিভীষণের সিদ্ধান্তকে “দুর্মতি” (মন্দ বুদ্ধি) বলে চিহ্নিত করে। |
আরও পড়ুনঃ সাম্যবাদী কবিতার মূলভাব ও ব্যাখ্যা প্রতি লাইনের
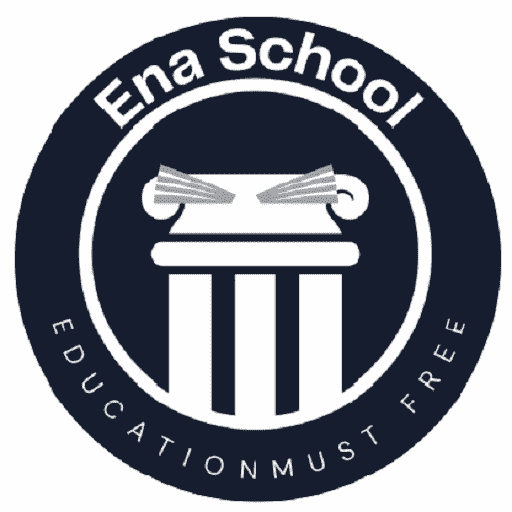
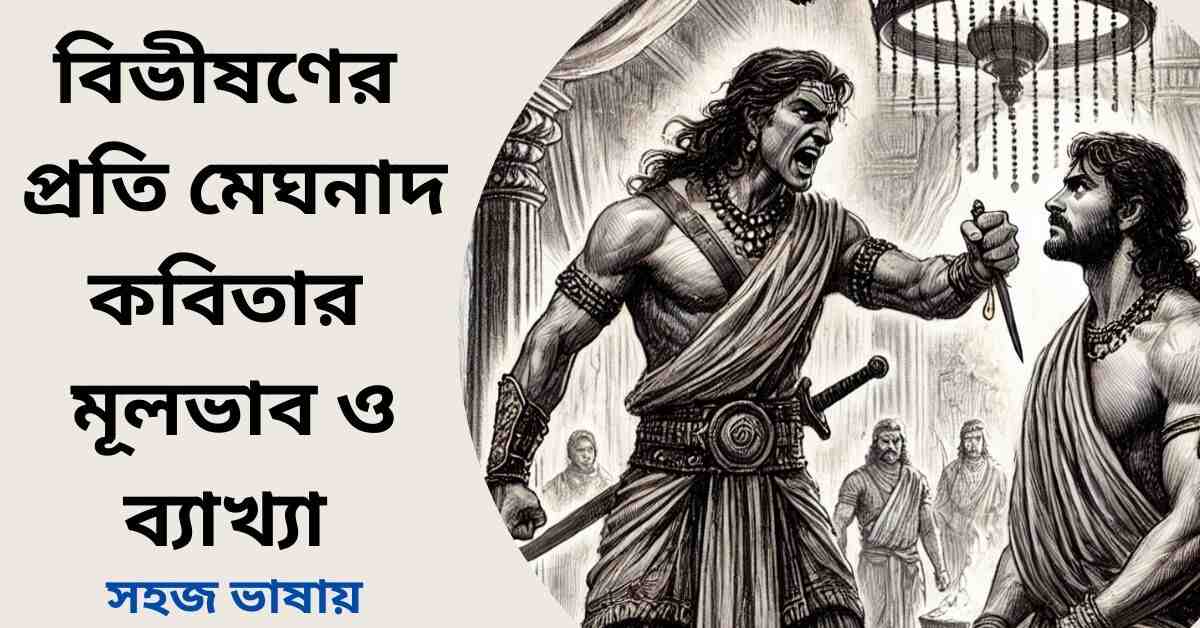
খুব সুন্দর।প্রতিটি লাইন ধরে ধরে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যে শব্দের অর্থ দূর্বদ্ধ সেটা অর্থ স্পষ্ট করা হয়েছে। এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী দু’ই উপকৃত হবে।